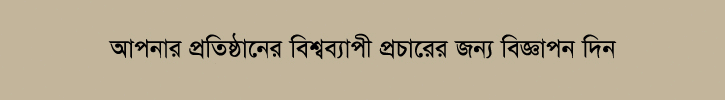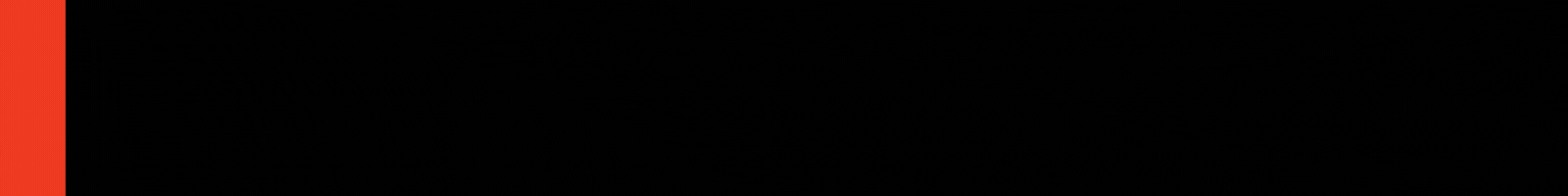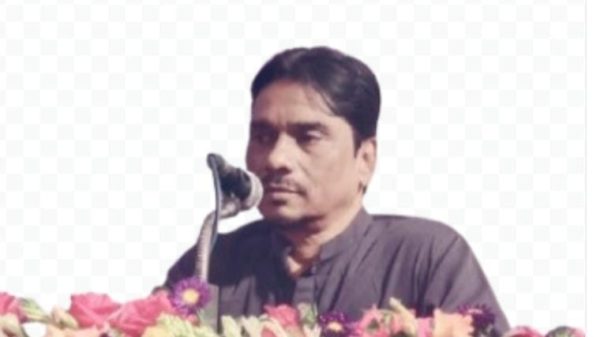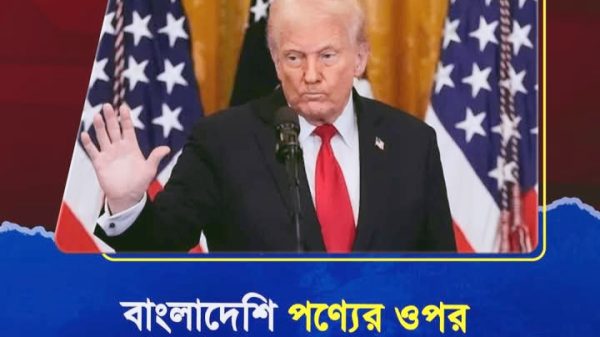অসংগতিতে ভরা নতুন কারিকুলাম।
- প্রকাশিত: বৃহস্পতিবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৪
- ২০৯ বার পড়া হয়েছে

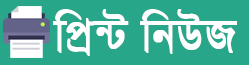
ডেস্ক রিপোর্টঃ
কারিকুলামকে উন্নতির নামে এ দেশের শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি বেখাপ্পা ও ধ্বংসাত্মক কারিকুলাম চালু হওয়ার দেড় বছরের অধিক সময় পার হওয়ার পর সারা দেশের দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, তথাকথিত স্মার্ট নাগরিক বানানো, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বানানোর এই কারিকুলামের মাধ্যমে যেটুকু লেখাপড়া ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। প্রতিদিন নিত্যনতুন নির্দেশনা দেওয়া ও বাতিল করা, কীভাবে মূল্যায়ন হবে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা এবং হযবরল নির্দেশনায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকরা নিরুপায় ও অসহায়। এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ কারোর কথাই শুনছে না। কেউ তাদের বলেনি যে, কারিকুলাম পরিবর্তন করতে হবে। এমনটি নয় যে, দেশে ডাক্তার, শিক্ষক, প্রকৌশলী তৈরি হচ্ছিল না। এমনও নয় যে, বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে শিক্ষার্থীরা যেতে পারছিল না। শিক্ষা যেভাবে চলছিল তার চেয়ে ভালোমানের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দরকার ছিল ভালো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, তাদের ভালো বেতন প্রদান করা, মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও দরকার ছিল তাদের স্বাধীনতা প্রদান করা। আরও প্রয়োজন ছিল স্কুল-কলেজের ওপর থেকে দুর্বৃত্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির অপসারণ ও প্রশাসনিক হয়রানি থামানো। কিন্তু তা না করে প্রতিনিয়ত শিক্ষার উন্নয়নের নামে যা করা হচ্ছে, তাতে শিক্ষার আরও পতন ঘটছে। কে বলেছিল এনসিটিবির দুই-চারজন কর্মকর্তার পুরো দেশের কারিকুলাম পুরো পরিবর্তন করার ক্রেডিট নিতে? তারা কজন যেন সবই বোঝেন, কারও কোনো কথা শুনতে চাননি। ফলে যেটি হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষায় আরও অধঃপতন ঘটেছে। এর প্রমাণ যে কেউ যে কোনো সময় দেশের বিদ্যালয়গুলো ঘুরে আসলে দেখতে পাবেন।
অনবরত নতুন নতুন সিদ্ধান্ত, শুধু জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য! যেমন—কোনো শিক্ষার্থী যদি এসএসসি পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয়, তাহলেও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। তবে তাকে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বিষয়ে পাস করতে হবে। আর তিন বা তার বেশি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে একাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা এমনিতেই ছেড়ে দিয়েছে, বিশেষ করে যারা পারিবারিকভাবে সিরিয়াস তারা বাদে। তারপর অকৃতকার্য হয়েও কলেজে ভর্তির সুযোগের মতো খবর তাদের অবস্থা যে আরও কোথায় নিয়ে যাবে, তা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখার সময় পাননি। কেউ কেউ বলছেন, ২০২৫ সালে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও মূল্যায়নের পর বোঝা যাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সেটি কতটা সফল। কিন্তু আমি বলছি সেই পর্যন্ত এই পুরো ব্যবস্থার মধ্যে যত শিক্ষার্থী আছেন এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই কিন্তু যে মহাক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং আরও হবে, সেই দায় নেওয়ার কিন্তু কেউ নেই। জাফর ইকবাল স্যার বলেছেন, এই কারিকুলামের সুফল দেখতে পাঁচ-সাত বছর সময় অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু স্যারের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখার কতটা সুযোগ হয়েছে জানি না, আমি কিন্তু দেখেছি এবং দেখে চলছি। উপকার যেটি হয়েছে, শিক্ষার্থীরা বই দেখে পড়তে পারছে না—বাংলা বইও না, ইংরেজিও না। ভাষা দিয়েই সব বিষয়ের বই লেখা, ভাষাতেই যদি তারা এত দুর্বল থাকে তাহলে কোথায় দক্ষতা আর কোথায় কম্পিটেন্সি অর্জন? তাদের সংখ্যা প্রায় শতাংশের কাছে। তারা এসব থেকে যোজন যোজন দূরত্বে অবস্থান করছে। আমরা কল্পনায় যা ভাবি যে, সব শিক্ষার্থী তাদের স্বাধীনতা নিয়ে শিখবে, আনন্দের মাধ্যমে শিখবে। যে পাঠ্যবই করা হয়েছে, তাতে আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই ব্যতিক্রমী দুয়েকটি অধ্যায় ছাড়া। নিজেরা সব চিন্তা করে নিজেরাই কল্পনায় দেখছি শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু শিখছে কিন্তু বাস্তবে কী হচ্ছে তার ধারেকাছেও যাচ্ছি না।
আমরা যারা শিক্ষা নিয়ে মাঠে কাজ করি, শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাভাবনা করি, বারবার বলে আসছি কারিকুলাম লিখিতভাবে খুবই ভালো কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এর মিল অনেক কম। এই কারিকুলামকে অর্থবহ করতে হলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ লিখিত পরীক্ষা থাকতেই হবে। আমরা যতই বলি না কর্তারা ততই শক্ত অবস্থানে চলে যাচ্ছিলেন যে, লিখিত পরীক্ষা মানে মুখস্থ, লিখিত পরীক্ষা মানে প্রাইভেট পড়া, লিখিত পরীক্ষা মানে নোট গাইডের ব্যবসা। কোনোটিই কিন্তু থেমে নেই, শুধু থেমে গেছে শিক্ষার্থীদের জানার আগ্রহ, বইপড়া, তাতে অবশ্য কর্মকর্তাদের তেমন কিছু যায় আসে না। কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনসব কথা বলেন বা ব্যাখ্যা দেন যে, এ দেশে শিক্ষা নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করেন তারা কেউ কিছু বোঝেন না। বোঝেন শুধু এনসিটিবির দুই-চারজন কর্মকর্তা, যারা লোকজন ধরে কলেজ থেকে ডেপুটেশনে ঢাকায় থাকার জন্য এনসিটিবিতে এসেছেন।
এ শিক্ষাক্রমে ফরমাল কোনো লিখিত পরীক্ষা না থাকায় শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে না। শিক্ষার্থীরা কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে নেই। অথচ একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাইল্ড বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হয়, পরীক্ষা বা পড়াশোনার অত্যধিক চাপ নয়, এক ধরনের তাগিদের মধ্যে থাকতে হয়। তা ছাড়া প্রতিযোগিতা যাতে অসুস্থতা সৃষ্টি না করে, সেটিকে কীভাবে পরিমার্জন করে সুস্থ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়, সেটি নিয়ে কাজ করার কথা। আমরা ফুটবল খেলা দেখি সেখানে প্রতিযোগিতা আছে, ক্রিকেট দেখি সেখানে প্রতিযোগিতা আছে। এভাবে সব কাজেই প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু নতুন কারিকুলামে আমরা বলছি, শিক্ষার্থীরা কোনো প্রতিযোগিতা করবে না। একজন খেলোয়াড় যদি জানে যে, তাকে কোনো গোল করতে হবে না, তাহলে সে কতক্ষণ খেলবে? সেই দশা হয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের। বইয়ে বলা হয়েছে, তারা আনন্দচিত্তে সারাদিন বইয়ের কাজ করবে কিন্তু পরীক্ষার চাপ তাদের সইতে হবে না। একটি বিষয়কে বারবার অনুশীলন করতে হয় বিভিন্নভাবে, লিখে, পড়ে, আলোচনা, উপস্থাপনা, রিপোর্ট রাইটিং ইত্যাদি করে। কিন্তু এখন যেটি হয়েছে, শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করার সময় পাচ্ছে খুবই কম। একজন শিক্ষককে বিশেষ করে বড় ক্লাসে ডিসিপ্লিন মেনটেইন করতেই সময় চলে যায়, কখন সে শিক্ষার্থীদের দিকে ব্যক্তিগতভাবে খেয়াল রাখবেন। এখানে আরেকটি কথা হচ্ছে, শিক্ষকদের নিজস্ব মূল্যায়ন এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়, শহর থেকে গ্রাম, ছোট শহর থেকে বড় শহর, ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে অপেক্ষাকৃত কম মানের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মূল্যায়ন কখনোই এক হবে না। আর এটি হবে না বলেই একটি জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড থাকতে হয়। বর্তমান কারিকুলাযে যে বিশাল গ্যাপটি রয়েছে, তার বহু প্রমাণের মধ্যে এটি একটি বড় প্রমাণ।
মাধ্যমিকের মূল্যায়ন পদ্ধতির শিখন ফলের পরিবর্তে পারদর্শিতার নির্দেশক বা পিআই দিয়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিকে প্রতিটি যোগ্যতার বিপরীতে তিন-চারটি শিখনফল আছে। কিন্তু মাধ্যমিকের যোগ্যতার বিপরীতে পিআইয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। প্রাথমিকে যোগ্যতার বিপরীতে শিখনফলের সংখ্যা দিয়ে সারা বছরের পাঠসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিকে পিআইয়ের সংখ্যা কম থাকায় সারা বছরের পাঠের সংখ্যার সঙ্গে তার মিল নেই। এই পিআই দিয়ে ধারাবাহিক কিংবা সামষ্টিক মূল্যায়ন কোনোটিই করা সম্ভব নয়, প্রাথমিকে শিখনফলের ওপর প্রতিটি পাঠ নির্ধারিত হয়েছে, যা দিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয় এবং ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক দেওয়া সম্ভব। পিআইয়ের সংখ্যা কম থাকায় মাধ্যমিকে সেই সুযোগ নেই। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফলাবর্তন প্রদান করা অর্থাৎ ফিডব্যাক দেওয়া। আর সামষ্টিক মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রেড প্রদান করা। প্রাথমিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিখনফল থেকে সহজেই প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু মাধ্যমিকের শিখনফল না থাকায় এবং তার ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক রচিত না হওয়ার কারণে পাঠ্যবই সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য উপযোগী নয়। ফলে পিআই দিয়ে সামষ্টিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। মাধ্যমিকের পিআইয়ের সংখ্যা কম থাকায় তা দিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করাও সম্ভব নয়। কারণ সেখানে ফলাবর্তন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে অধ্যায় শেষে, মাস শেষে প্রদান করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো রেকর্ড কিপিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। প্রাথমিকে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক আর প্রজেক্ট অ্যাসাইনমেন্টের নামে শিক্ষা ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সারারাত মোবাইল টিপে অ্যাসাইনমেন্ট করছে। মোবাইল দেখে দেখে যদি অ্যাসাইনমেন্ট করতে হয়, তা নোটবইয়ের চেয়ে কম কীসে? এক অভিভাবক বললেন, সপ্তম শ্রেণিতে ছয় দফার ওপর অ্যাসাইনমেন্ট করতে বলা হয়েছে তার সন্তানকে। কীভাবে করবে কোনো গাইডলাইন নেই। শিক্ষক নাকি বলে দিয়েছেন গুগল সার্স করে বের করতে। বইয়ে তিনটি প্রশ্ন আছে—কবে ছয় দফা হয়েছে, কে ছয় দফা দিয়েছে, কোথায় দিয়েছে। বাচ্চাদের অ্যাসাইনমেন্টের নামে এসব করতে দেওয়া হচ্ছে, তাদের তথ্য জানতে বলছে নিকটবর্তী লোকজনের কাছ থেকে। তারা কাকে জিজ্ঞেস করবে আর কেইবা তাদের সঠিক উত্তর দিতে পারবে তার কোনো হদিস নেই। বিজ্ঞান ও গণিতে গুরুত্ব তো অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার অনেক কিছু করে, যা জনগণকে মানতে বাধ্য করা হয়, জনগণের প্রচুর কষ্ট হয় কিন্তু ওইসব সরকার আত্মতৃপ্তিতে ভোগে। যেমন আমাদের দেশের বাজেট। বাজেটের গন্ধ পেলেই সব জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়, সাধারণ মানুষের ত্রাহি ত্রাহি ভাব আর কর্তারা জনগণকে উপহাস করে বলতে থাকেন—এটি স্বস্তির বাজেট। পরিমাণে আগের চেয়ে কমিয়ে জীবনের কষ্টের ওপর দিয়ে তারা চালিয়ে যান আর কর্তারা বলতে থাকেন জনগণের মঙ্গলের বাজেট। জনগণের কিছুই করার নেই। কিন্তু কারিকুলামের কী হলো? এটা তো জনগণ চায়নি। এটাও কি বাজেটের মতো চাপিয়ে দেওয়া হলো? যাদের জন্য কারিকুলাম, যারা এ কারিকুলাম বাস্তবায়ন করবেন তাদের কথা না শুনে কেন এই কারিকুলাম চালু করা হলো?
লেখক: শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক
প্রেসিডেন্ট: ইংলিশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইট্যাব)
সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর-ভাব বাংলাদেশ